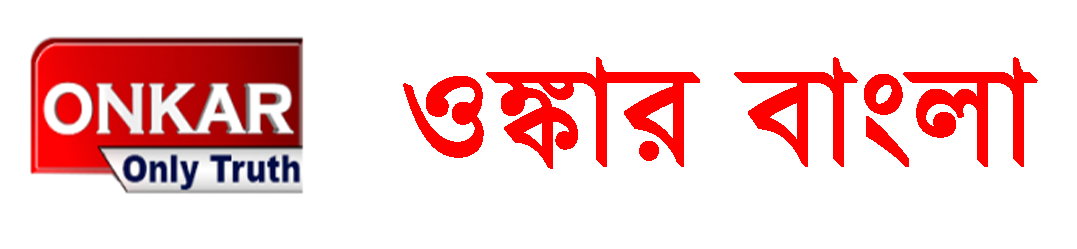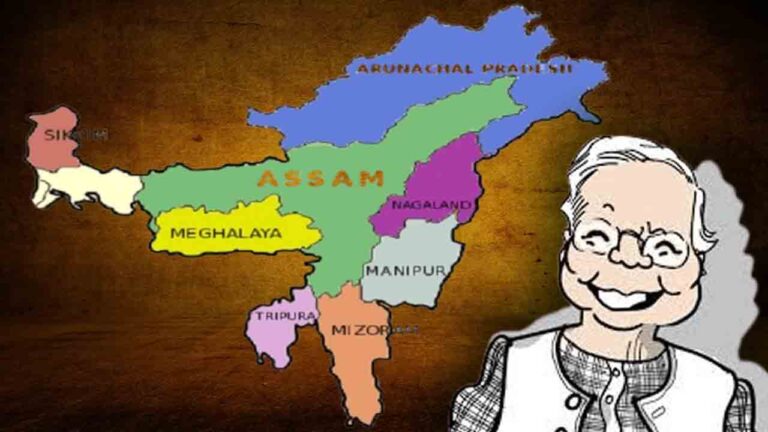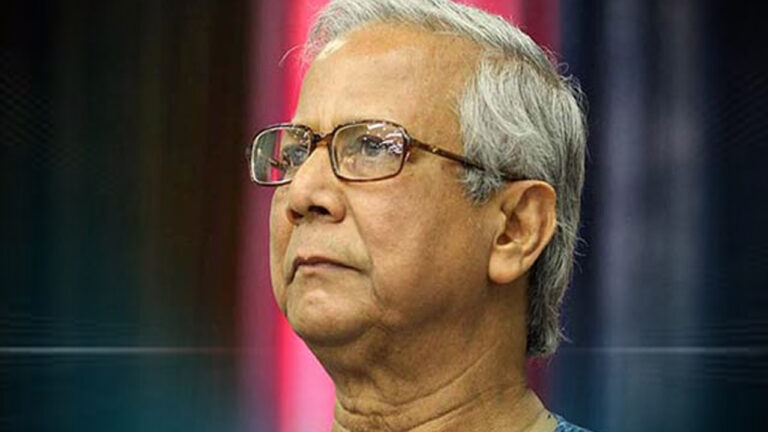গৌতম রায়
পর্ব-১
মায়ের গানের খাতায় পেয়েছিলাম লাইনটা, ‘বাতাসে ভাসিছে বাতাবী ফুলের গন্ধ। বনে বনে জাগে ঝিল্লি নূপুর ছন্দ’। গানটার শুরুটা ছিল, ‘জেগে আছি একা, জেগে আছি কারাগারে’- গানটা রেকর্ড করেছিলেন সত্য চৌধুরী। ‘পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমায়’-এর সেই কালজয়ী শিল্পী। কিন্তু রেকর্ডে আমি গানটা প্রথম শুনি ফিরোজা বেগমের কন্ঠে। কমল দাশগুপ্তের সুরের কিছু কালজয়ী গান আবার গেয়েছিলেন ফরিদপুরের ফেণী, যাঁর পোষাকী নাম ছিল ফিরোজা।
ছোটমাসীর কাছে বায়না করে নৈহাটি সিনেমা হলের পাশের গলিতে ওয়াচ এন টিভির দোকান থেকে ফিরোজা বেগমের ওই লং প্লেইং রেকর্ড টা কিনেছিলাম। এই রেকর্ডে, ‘বাতাসে ভাসিছে বাতাবী ফুলের গন্ধ’ শোনবার আগে সত্যিই বাতাবী ফুলের গন্ধে যে বেহেশতের খুশবু আছে — সেটা কখনও অনুভব করবার চেষ্টাই করি নি।
আমার দিদিমার বাড়িতে একটা বাতাবী লেবুর গাছ ছিল। গাছটা ছিল আমার দিদি ছোট্ট যে খুপড়ি ঘরে, গরমে হাপসাতে হাপসাতে পড়ত, যে ঘরটাকে আমরা ‘নোতুন ঘর’ বলতাম তার ঠিক সামনে ছোট্ট এক টুকরো জমির উপরে। তার পাশে ছিল ছোট একফালি সিমেন্ট বাঁধানো চাতল। সেই চাতালের বাঁ দিকে ছিল ওই বাতাবী লেবুর গাছটা।
নতুন ঘরের পাশে ছিল আর একটা ছোট ঘর। ঘরের চাল ছিল টিনের। কেন যে এই ঘর দুটো ছোটমামা করিয়েছিল তার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছোটকাল থেকে বুড়ো বেলা পর্যন্ত শুনি নি। তবে ছোটমামার এসব কাজের পিছনে আমার দিদিমাকে তাঁর বিয়েতে পাওয়া তাগার একটা খেসারত দিতে হয়েছিল। কারণ, পাছে ঘর করে দেওয়ার খোটা ছোটছেলে দেয়, তাই দিদিমা নিজের ছেলের কাছেও কখনও এতটুকু ঋণ রাখতে চান নি।
শুনেছি ওই ঘরগুলো তৈরি হওয়ার আগে ওখানটায় ছিল গৈল ঘর। মানে গোয়াল। মধ্যবিত্ত বাড়িতে গরু রাখার বিলাসিতাটা আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে মফঃস্বলের বাঙালি বাড়িতে একটু বেশি মাত্রায়ই ছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশষে তখন অনেক বাঙালি বাড়িতেই এটা ছিল দস্তুর।
আসলে দেশভাগ তখন একটা সেটেল্ড ফ্যাক্ট। দেশভাগের আগে বা অল্প কিছু সময় পরে ‘গোরু’ ঘিরে রাজনীতির যে তাপ উত্তাপ তখন সময়ের দাবিতেই তা বেশ অনেকটা মিইয়ে গেছে। সেই জলেভেজা, ন্যাতানো আগুনকে উস্কে দেওয়ার মত অপরাজনীতি তখন ও চেগে ওঠার সময় পায় নি।
এমন কালে যে শহরে আমি তখনও বড় হয়ে ওঠার সুযোগই পাইনি, সেই শহরে বা তার পাশের শহরে ব্রাহ্মণ্যবাদ সমস্ত রকমের মানবিক সম্পর্কগুলো ঢেকে দেওয়ার জন্যে সবরকমের পাঁয়তারা তখন কষে ফেলেছিল। আমার শহর ভাটপাড়ার বামুন ধারার দুটো স্রোত ছিল। একটা হল পাশ্চাত্য বৈদিক ধারা। অপর ধারা হলো দাক্ষিণাত্য বৈদিক। এই অবাঙালি বামুনের দল বাঙালিয়ানার অ আ ক খ জানত না। এখনও জানে না।
যাক সে সব কথা। গোরু ঘিরে হিন্দু-মুসলমানের আজকে যে আকচা আকচি তৈরি হয়েছে সেসব ঘিরে তখনও কিছু তৈরি হয় নি। গেরস্ত বাড়িতে গোরু পোষে খাঁটি দুধ খাবে বলে। গোরুর যত্ন আত্তি করে সাধ্য মত। গাঁয়ে গেরস্ত নিয়েই গায়ে গতরে খাটে গোরুকে নিয়ে। একটু পয়সাওয়ালা লোক হলে গোরুর দেখভালের জন্যে লোক রেখে দেয়। গাঁয়ের এতিম ছেলেদের জন্যে এই গোরু-ছাগল দেখার কাজটা অনেক সময়েই নির্দিষ্ট থাকে।
শুনেছি আমার দিদিমার বাড়িতে যখন গোরু ছিল, বাইরের মাইনে করা লোক ছিল দেখভালের জন্যে। খাবার দেওয়া, গোয়ালঘর পরিস্কার করা এসব কাজের জন্যে হিন্দিভাষী একজন ছিল। দুধ দুয়ে দিতো দুবেলা একজন মহিলা।তাঁর নাম ছিল রাধা।
রাধার দাদা ছিলেন আমাদের শহরে রবীন্দ্রনাথকে চেনবার আতস কাঁচ। আর গোবিন্দ মাষ্টারমশাই, তিনি আমাদের মায়ের মাষ্টারমশাই ছিলেন। আমরাও যখন ক্লস সেভেনে উঠি, উনি অবসর নেন। সৎ, ভালো মানুষের সংজ্ঞা হিসেবে ছোটবেলায় বাড়িতে যে দু’ একজনের নাম উচ্চারিত হতো, যাঁদের আদর্শকে জীবন গড়ে তোলবার কথা আমাদের শেখানো হতো, গোবিন্দ স্যার ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।
গোবিন্দ স্যারের বোন ছিলেন এই রাধা। থাকতেন কৈবত্যপাড়াতে। ছোট্ট বাড়িটা মনে হয় নিজেরই ছিল। ‘কৈবত্যপাড়া’ নামটা শুনলেই বোঝা যায় জাত্যাভিমানের কী দাপট ছিল আমাদের শহরে সেকালে। জাত্যাভিমানের দাপট থাকলেও সেই ‘নীচুজাতে’র লোকেদের জমি জিরেত ছলে বলে কৌশলে হাতিয়ে নিতে কিন্তু কোনও অসুবিধা হতো না এখানকার ভটচার্যি বামুন ঠাকুরদের।
হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ওই কৈবত্যপাড়াতে একটা বিরাট মাঠ নামমাত্র টাকায় কিনে নিয়েছিল। পরে নিজের মেয়েদের মধ্যে সে জমি ভাগ বাটোয়ারা করে দেয়। নিজের দাদা মরে যাওয়ার পর ডেড বডির টিপ ছাপ নিয়ে দানপত্র তৈরি করে দাদার হয়ে। সেই দানপত্রে দেখা যায়, ওই ডাক্তারের দাদা, নিজের দুই মেয়েকে নিজের ভাগের বিষয় সম্পত্তির কানাকড়িও দেয়নি। সব দিয়েছে ভাইয়ের ছেলেকে।
সেসব অনেক গল্প। তা এই কৈবত্যপাড়া নামটা এখন আর টিকে নেই। সরকারি দলিল দস্তাবেজে কি আছে কে জানে। তবে লোকের মুখে মুখে সেটা এখন বাবুরাণীপাড়া। তবে পৌরসভা রাস্তার নামের যে বোর্ড সেঁটেছিল বেশ কিছুকাল আগে সেখানে বাবুরাণীপাড়া লেখা ছিল না। ছিল, ‘কৈবত্যপাড়া’। তখন মনে হয়েছিল, এককালে বামপন্থীরা যে সামাজিক জাগরণের একটা কাজ হিসেবেই এই জাতপাত ভিত্তিক নামকরণগুলোকে বদলাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিছুটা সফল ও হয়েছিলেন। সেই বামপন্থীদের হাতে পরিচালিত পৌরসভা কেন এতটুকু সচেতনতার পরিচয় দেবে না এমনতরো সাইনবোর্ড সাঁটবার সময়ে ? হ্যাঁ, এমন সাইনবোর্ড লটকাবার কালে আমাদের স্থানীয় পৌরসভাটি ছিল কিন্তু বামপন্থীদের দ্বারাই পরিচালিত।
মুক্তোপুরের খাল, সাধু উচ্চারণে মুক্তারপুরের খাল- তার পাশেই রাসমেলার মাঠ। পাশের শহরের বেশ জমি জিরেতের মালিক মুখার্জীবাবুদের সম্পত্তি। আই সি এস অশোক মিত্র সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা গ্রন্থেও এই রাসমেলার কথা আছে। ছয়ের দশকের শেষদিক পর্যন্ত রাসমেলা বসতো জমিয়ে। তারপর কেন যে বন্ধ হয়ে গেল- তার সঠিক ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেন না। তবে যেটা মনে হয়, মেলাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যে মুখুজ্জেদের শরিকি বিবাদই দায়ী।
মেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অনেককাল পরে ওই মাঠে বানজরার দল মাঝে মাঝেই ভিড় করতো। অস্থায়ী ভাবে বাস করতো তারা ঝুপড়ি করে। এই বানজারাদের মধ্যে কাকমারা থাকতো অনেক। কাকশিকার ছিল তাদের পেশা। সেইসঙ্গে টিয়াপাখিও ধরতো।দেশীয় পাখি ঘিরে আইনকানুন তখন ও হয় নি। ফলে অনেকেই এদের কাছ থেকে টিয়াপাখি কিনতো। আর কাক ঘিরে ছিল এই কাকমারাদের বিচিত্র জীবন যাপন। কাকের পালক, ঠোঁট – এসব দিয়ে তারা তৈরি করতো নানা রকমের জড়িবুটি। দেহাতী লোকেদের মধ্যে সেসব জড়িবুটির বেশ জনপ্রিয়তাও ছিল। নানারকম রোগ থেকে শুরু করে বন্ধ্যাত্ব– সবকিছুর এই জড়িবুড়ি, পশুপাখির হাড়গোড়ের চিকিৎসা ছিল বানজারাদের কাছে মজুত।
বানজারারা এই রাসমেলার মাঠে নিজদের থাকার ঝুপড়ির বাইরে ছোট একটা তাঁবু ফেলতো। বেশ রঙিন কাপড় চোপড় দিয়ে দেখনদারি ভাবেই তৈরি হতো সে তাঁবু। ভেতরটা সুন্দর ঝকমকে কাপড় দিয়ে মোড়া থাকতো। তাঁবুর গায়ে থাকতো নানা মরা পশুপাখির মুখ। কখনো সখনো বাঘের মুখ ও কোনও কোনও দলের থাকতো। বহু রকমের রুদ্রক্ষ, তার মালা।হরেক কিসিমের পাথর। পাথরের মালাও থাকতো। পশুর সিং থাকতো।
এসব ছিল তাদের চিকিৎসার উপকরণ। চটকলের শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরাই কেবল নয়, গেরস্ত ঘরের ছেলেমেয়েরাও ওইসব পশুপাখির মাথা দেখতে ভিড় জমাতো। ছোট্ট হান্ড মাইকে একটা কেমন তরো হিন্দিতে ওই তাঁবুর লোকেরা সব অসুখ বিসুখ সারানোর বিজ্ঞাপন করতো। দেহাতিদের সঙ্গে মেলামেলার দরুণ ভোজপুরি হিন্দি ভালো না বলতে পারলেও কিছুটা বুঝতে পারতাম। কিন্তু ওই বানজারারা যে কি বলতো- তার একবর্ণ ও উদ্ধার করতে পারতাম না। সমবয়ষ্ক দু’ চারটে দেহাতি ছেলেমেয়েদের কাছে জানতে চাইতাম; কি বলছে ওরা ?
দেহাতি ছেলেমেয়েরাও ঠিক মত বুঝে উঠতে পারতো না ওইসব কাউয়ামারা লোকজনদের কথাবার্তা। দেহাতিরা কেবল বলতো; সব বিমার কে ইনলোগোমে ইলাজ করেগা। অর্থাৎ, এই লোকেরা সব অসুখের চিকিৎসা করবে।
একটু বড়ো হয়ে বুঝতে পারলাম, চটকলের শ্রমিকদের মধ্যে কেউ কেউ বেপাড়া যাওয়ার দৌলতে নানা রকম রোগে ভোগে। সেসব রোগ ঘিরে ঠিক মত ডাক্তারদের কাছে যাওয়ার ভাবনা তখনও ওইসব কুলি মজুরদের মধ্যে হয় নি। না হওয়ার কারণ যে সামাজিক লজ্জা, তা কিন্তু নয়। কারণ, স্থানীয় মানুষজনদের সঙ্গে এই চটকলের কুলিকামিনদের দুরত্বটা এতটাই ছিল যে, ওরা বাঁচলো কি মরলো- তা নিয়ে স্থানীয় ভদ্দরলোকেদের এতটুকু মাথা ব্যথা ছিল না। আর একা থাকে এসব কুলি মজুর রা। বৌ থাকে দেহাতে হাজার মাইল দূরে। তাই সুরো ভট্ চাযের গলিতে এরা যাবেই– এটা ছিল সেসময়ের সামাজিক বিন্যাসে একদম টেকন ফর গ্রান্টেড।
বানজরাদের কাছে যৌন চিকিৎসার জন্যে ভিড় করা ভিন রাজ্যের, ভিন ভাষার লোকজনেরা আদৌ কোনও শারীরিক যন্ত্রণা থেকে রিলিফ পেতো কি না কে জানে ! তবে ওসব জড়িবুটির কারিকুড়িতে তাদের রোগ আরো জটিলই হয়েছে বলে মনে হয়।
( চলবে)